ভাষা আন্দোলনে সংবাদপত্র ও সম্পাদকের ভূমিকা
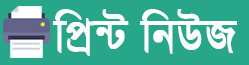
দেশভাগের আগে ঢাকাকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার ব্যাপ্তি খুব একটা বিস্তৃত ছিল না। এ সময়ের প্রধান ও প্রভাবশালী বাংলা সংবাদপত্র আজাদ ও ইত্তেহাদ প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। যদিও ঢাকায় এই সংবাদপত্র দুটির প্রচুর পাঠক ছিল। সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিসহ নানা বিষয়ে মানুষের মনোভাব গঠনের সংবাদপত্র দুটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।
১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরপরই কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল আজাদ। আর ইত্তেহাদ অন্তত চারবার ঢাকায় চলে আসার আবেদন করলেও মুসলিম লীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলে তা আটকে যায়। ফলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রতিষ্ঠিত এই সংবাদপত্রটির কলকাতাতেই অকালে বন্ধ হয়ে যায়।
ইত্তেহাদ-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৪৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করা সংবাদপত্রটি সম্পাদক ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, লেখক ও সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ। এটা ছিল বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক কাঠামোর একটি উন্নত সংবাদপত্র।
যাত্রা শুরুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সংবাদপত্রটি কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর সংবাদপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের পরই ছন্দপতন ঘটে। ওই সময় অনেক শিক্ষিত মুসলিম কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। তাই ইত্তেহাদ-এর পাঠক কমে যায়। যদিও ঢাকার পাঠকের কথা চিন্তা করে সংবাদপত্রটির ব্যবস্থাপনা বিভাগ ওরিয়েন্টাল এয়ারওয়েজের মাধ্যমে সংবাদপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল।
পরে মুসলিম লীগ সরকার সেটাও বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ১৯৫০ সালের গোঁড়ার দিকে পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই সংবাদপত্রটি বাংলা ভাষার পক্ষে তাদের জোরালো অবস্থানের জানান দিয়েছিল। যার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারকের ভূমিকা রাখেন সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ।
এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত ক্ষণ ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি হলেও কয়েক বছর আগে থেকেই ভাষার প্রশ্নে আলোচনা শুরু হয়েছিল। যে বিষয়ে জনমত গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল কিছু সংবাদপত্র। তবে এর বিপরীতে কিছু সংবাদপত্র ও সম্পাদক যে বাংলা ভাষার বিরোধী ছিলেন সেটাও ঐতিহাসিক সত্য।
ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত ক্ষণ ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি হলেও কয়েক বছর আগে থেকেই ভাষার প্রশ্নে আলোচনা শুরু হয়েছিল। যে বিষয়ে জনমত গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল কিছু সংবাদপত্র।
প্রথমে আসা যাক, ইত্তেহাদ ও আবুল মনসুর আহমদের ভূমিকায়। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই ইত্তেহাদ প্রকাশ করে বাংলা ভাষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সব লেখা। ১৯৪৭ সালের ২২ ও ২৯ জুন দুই কিস্তিতে ইত্তেহাদ-এর পাতায় প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ আবদুল হকের প্রবন্ধ ‘বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব’।
উল্লেখ করা যেতে পারে, ভাষার পক্ষে এই লেখাগুলো প্রকাশে শুধু আগ্রহী ভূমিকা পালনই নয়, ইত্তেহাদ এর সম্পাদকীয়তে বাংলা ভাষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ। যদিও ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে যখন ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটেছে তখন ইত্তেহাদ খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ ১৯৪৮ সালে সংবাদপত্রটি পূর্ব বাংলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আর ১৯৫২ সালের আগেই সংবাদপত্রটির অকাল মৃত্যু ঘটে।
আসা যাক, আজাদ-এর ভূমিকায়। ১৯৩৫ সালে কৃষক প্রজা পার্টির শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নতুন একটি সংবাদপত্র প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেন। সেই তাগিদ থেকেই ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল আজাদ। যার সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা ও সাংবাদিক মওলানা আকরাম খাঁ।
তিনি ছিলেন সেই সময়ের মুসলিম জাগরণের পক্ষে অন্যতম সোচ্চার কণ্ঠস্বর। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনেও তার বড় ভূমিকা ছিল। চরিত্রগতভাবে আজাদ মুসলিম জাগরণ ও পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও বাংলা ভাষার প্রশ্নে অনেক সময় ঐতিহাসিক ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে আজাদ এর ভূমিকা যে বাংলা ভাষার বিপক্ষে ছিল সেটাও ঐতিহাসিক সত্য।
১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বাংলা ভাষার পক্ষে আজাদ-এ প্রকাশিত হয়েছিল ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি বিশেষ লেখা। তাতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, ‘ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন আমি একজন শিক্ষাবিদ রূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি বিগর্হিতও বটে।’
পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ভাষার প্রশ্নে পরিষ্কার অবস্থান নিলেও পরে সংবাদপত্রটির ভূমিকা বদলে যায়। অনেকটা উর্দুর পক্ষে অবস্থান নেয় সংবাদপত্রটি। তাই ভাষা আন্দোলনে মওলানা আকরাম খাঁ’র আজাদ-এর ভূমিকা ছিল অনেকটা রহস্যজনক ও দ্বিধান্বিত। যদিও ১৯৫২ সালে গুলি করে ছাত্র হত্যার পর এই দ্বিধা কেটে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয় আজাদ।
ওইদিন বিকেলে আজাদ টেলিগ্রাম প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল ‘ছাত্রদের তাজা খুনে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত’। মুসলিম লীগ সরকার এই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে। তখনকার আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পদত্যাগ করেন প্রাদেশিক পরিষদ থেকে।
ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের এই প্রতিবাদ সে সময় ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করেছিল। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পদত্যাগ পত্রে লিখেন, ‘যে নুরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক, এ ব্যাপারে তাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এই দলের সহিত যুক্ত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসেবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।’
২৩ ফেব্রুয়ারি আজাদ প্রকাশ করে ‘পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের পরিষদ সদস্য পদে ইস্তফা’ শিরোনামের সংবাদ।
শুধু তাই নয় আবুল কালাম শামসুদ্দীন পরের দিনগুলোয় ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় অংশে প্রতিবাদী অনেকক্ষেত্রে বিপ্লবী শিরোনামের সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, ‘তদন্ত চাই’, ‘ভুলের মাশুল’, ‘পদত্যাগ করুন’, ‘সাফল্যের সূচনা’ ইত্যাদি।
ভাষার পক্ষে এই লেখাগুলো প্রকাশে শুধু আগ্রহী ভূমিকা পালনই নয়, ইত্তেহাদ এর সম্পাদকীয়তে বাংলা ভাষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ।
১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত অন্যতম ইংরেজি সংবাদপত্র ছিল পাকিস্তান অবজারভার। এই সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন আবদুস সালাম, মালিকানা ছিল হামিদুল হক চৌধুরীর। মালিক মুসলিম লীগ নেতা হলেও ভাষা আন্দোলনে সংবাদ যথাযথ গুরুত্বের সাথে প্রকাশে তিনি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াননি। বরং ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ভূমিকা রাখার জন্য পাকিস্তান অবজারভার এর সম্পাদক আবদুস সালাম ও মালিক হামিদুল হক চৌধুরী গ্রেফতার হয়েছিলেন। পাকিস্তান অবজারভার এর প্রকাশনাও বন্ধ করে দিয়েছিল নুরুল আমিনের প্রাদেশিক সরকার।
১৯৫২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অন্যতম সংবাদপত্র ছিল দৈনিক মিল্লাত। এটি মুসলিম লীগের বাম ঘরানার রাজনীতিবিদদের মুখপত্র ছিল। এর নেপথ্যে ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম। শুরুতে সংবাদপত্রটির সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ ইদরিস। আর ১৯৫২ সালে সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মো. মোদাব্বের। গুলি করে ছাত্র হত্যার পর মিল্লাত শিরোনাম করেছিল ‘রাতের আঁধারে এত লাশ যায় কোথায়?’ এই শিরোনাম প্রকাশের পরই মিল্লাত সম্পাদকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল।
ভাষা আন্দোলনে ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রতিবাদী ভূমিকা রেখেছিল সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সৈনিক। ট্যাবলয়েড আকারের চার পৃষ্ঠার এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটির সম্পাদক ছিলেন আবদুল গফুর। ছাত্র হত্যার পর সাপ্তাহিকটি লাল কালিতে শিরোনাম করে ‘শহীদ ছাত্রের তাজা রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত’। ঢাকার বাইরের এই প্রতিবাদও সহ্য করেনি নুরুল আমিন সরকার। ২৩ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হয়েছিলেন সাপ্তাহিক সৈনিক এর সম্পাদক আবদুল গফুর ও প্রকাশক প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম।
১৯৫২ সালের বাস্তবতায় একজন সম্পাদক ছিলেন একটি সংবাদপত্রের সবকিছু। তাকে সামনে রেখেই সবকিছু পরিচালিত হতো। তখন সংবাদপত্র অফিসে শ্রমবিভাগ কম ছিল, সংবাদপত্রের প্রতিবেদকরা বর্তমান সময়ের মতো সংবাদমাধ্যমের মুখপত্র ছিলেন না। সংবাদপত্রের প্রধান ব্যক্তি ও মুখপত্র ছিলেন সম্পাদক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখা সেইসব সম্পাদকদের প্রতি অতল শ্রদ্ধা।
গ্রন্থ সহায়ক:
১। ধর, সুব্রত শংকর (১৯৮৬), বাংলাদেশের সংবাদপত্র। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।
২। ধর, সুব্রত শংকর (২০১৫), বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস। ঢাকা: পিআইবি।
৩। ভট্টাচার্য, ড: নন্দলাল (২০১৯) সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত, কলকাতা: লিপিকা।
৪। রায়, সুজিত (২০১৮), সংবাদ সাংবাদিক সাংবাদিকতা। কলকাতা: দে পাবলিকেশন্স।
৫। হায়দার, জুলফিকার (২০১৭), বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশন।
রাহাত মিনহাজ ।। সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
minhaz_uddin_du@yahoo.com




























