‘বাংলার নববর্ষের ইতিহাসের কলঙ্কিত অতীত’
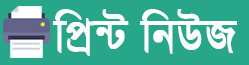
আজ আমরা যেভাবে পহেলা বৈশাখকে উৎসবের দিন হিসেবে উদযাপন করি, সেটি মূলত এক ধরনের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ফল। অথচ এই নববর্ষ উৎসবের পেছনে লুকিয়ে আছে বেদনার এক দীর্ঘ ইতিহাস, রক্ত, চোখের জল ও শোষণের কাহিনি, যা আমরা আজ প্রায় ভুলে গেছি বা ভুলে যেতে চেয়েছি।
বাংলার পহেলা বৈশাখ একসময় শুধুমাত্র ধনী জমিদার ও বণিক শ্রেণির মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ কৃষক ও প্রজাদের জন্য এটি ছিল না কোনো আনন্দের দিন, বরং এক ভয়ের প্রতিচ্ছবি। ৩০ চৈত্র ছিল জমিদারদের নির্ধারিত খাজনা আদায়ের শেষ দিন। সেইদিনটি ঘিরেই শুরু হতো নানা চাপ, শোষণ ও নিপীড়নের পালা। মরা মাস চৈত্রে ফসল কম হতো, ফলে প্রজাদের হাতে থাকত না খাজনা দেওয়ার টাকা। আর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জমিদার-মহাজন ও ব্যবসায়ীরা চালাতেন সুদখোরি ও দখলদারির নিষ্ঠুর খেল।
চড়ক সংক্রান্তি নামে পরিচিত এক প্রথাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল জমিদারদের এই আদায়ের কৌশল। এই দিনে প্রজাদের উপর চালানো হতো বর্বর অত্যাচার—বড়শি গাঁথা, বাণ ফোঁড়া ইত্যাদি নৃশংস প্রথার মাধ্যমে। শরীরে বড়শি গেঁথে ঘোরানো হত মানুষকে, তা-ও জনসমক্ষে, যেন এক প্রকার সতর্কবার্তা। জমিদারদের মুখে যদিও এটি ছিল ‘উৎসব’, আদতে এটি ছিল এক ভয়াবহ মানসিক চাপের প্রক্রিয়া—প্রজাদের মনে খাজনা না দেওয়ার ফলে কী পরিণতি হতে পারে, তা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।
এই তথাকথিত উৎসবকে ঘিরে জমিদারবাড়িতে আয়োজন করা হতো কবিগান, লাঠিখেলা, হরিনাম সংকীর্তন, মেলা ও পাঁঠাবলির। এগুলোর সবকিছুই ছিল কৌশলগত এক প্রচেষ্টা—প্রজাদের উৎসবে টেনে এনে খাজনা আদায় নিশ্চিত করা। জমিদাররা এই দিনেই একবার গর্বভরে সাধারণ প্রজাদের সামনে আসতেন, যেন একটি ‘রাজসিক প্রদর্শনী’। বলা হতো, যদি এই দিনে প্রজারা সম্পূর্ণ সাল তামামির খাজনা দিয়ে দেয়, তবে কোনো সুদ দিতে হবে না। আর তাতেই দলে দলে প্রজারা জমিদারবাড়িতে আসতে বাধ্য হতো।
কিন্তু যারা দিতে পারত না? তাদের ওপর নেমে আসত লাঠিয়াল বাহিনীর অত্যাচার। অনেক কৃষক আত্মহত্যা পর্যন্ত করতেন অপমান ও অনিশ্চয়তার যন্ত্রনায়। জমিদারদের এই শোষণের গল্প তুলে ধরেছেন গবেষক আখতার উল আলম, যিনি কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশালসহ পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে এই নৃশংসতার প্রমাণ পেয়েছেন।
প্রথাটি এতটাই ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল যে ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তা বন্ধ করতে চেয়েছিল। তবে এর সূচনা আরও পুরোনো—১৪৮৫ সালে রাজা সুন্দরানন্দ ঠাকুরের রাজ্যে। তখনও এটি ছিল রাজপরিবারভিত্তিক এক ধরনের আচার, যা পরে ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে।
তথ্য বলছে, এই সময়টিকে ঘিরেই জমিদাররা ‘লোকপাল’ নামে পরিচিত দেবতা শিবকে কেন্দ্র করে পূজার আয়োজন করতেন, যেন উৎসবের সঙ্গে ধর্মীয় আবহও তৈরি হয়। এ ছিল মানুষের মনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলবার আরেকটি কৌশল। যেন বিনোদন, ধর্ম, ভয়—সবকিছুর মিশেলে প্রজাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
সেই সময়কার বাস্তবতা সম্পর্কে পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি তাঁর ‘পূজা-পার্বণ’ গ্রন্থে বলেছেন, “কয়েক বৎসর হইতে পূর্ববঙ্গে ও কলিকাতার কেহ কেহ পয়লা বৈশাখ নববর্ষোৎসব করিতেছেন। তাহারা ভুলিতেছেন, বিজয়া দশমীই আমাদের প্রকৃত নববর্ষ।” তাঁর মতে, পহেলা বৈশাখ বণিক শ্রেণির জন্য ছিল, সমাজের জন্য নয়। কারণ নতুন খাতা খোলা, দেনা আদায়ের জন্য ক্রেতাদের নিমন্ত্রণ করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। নতুন কাপড় পরা বা আনন্দ করার তেমন কোনো চিহ্ন ছিল না এই দিনে।
আসলে, বাংলার প্রকৃত নববর্ষ ছিল অঘ্রাণ মাসে—নবান্ন উৎসবের মাধ্যমে। কৃষকের ধান উঠত সেই সময়, ঘরে আনত সোনালি ফসল। তখন ছিল উৎসবের আমেজ। কিন্তু মুঘল সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে সৌর ও চন্দ্র বছরের পার্থক্য ঘোচাতে বৈশাখ মাসে নববর্ষ চালু করেন। পরবর্তীতে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালুর মাধ্যমে জমিদার শাসনের যাঁতাকলে পড়ে এই নববর্ষ হয়ে ওঠে প্রজাদের জন্য ভয় ও নির্যাতনের দিন।
আজকের দিনে আমরা যখন পহেলা বৈশাখে আনন্দ করি, মেলা করি, সংস্কৃতির জয়গান করি—তখন ইতিহাসের এই অন্ধকার অধ্যায়টিও মনে রাখা জরুরি। যাতে উৎসব কখনও শোষণের রূপ না নেয়, আর আনন্দের আড়ালে কোনো চোখের জল লুকিয়ে না থাকে।
তথ্যসূত্র:
১। নববর্ষ ও বাংলার লোক সংস্কৃতি, আখতার-উল-আলম, পৃষ্ঠা – ১৩
২। https://prohor.in/story-of-an-old-tradition-of-bengal
৩। https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/polatokmurg/30296132















